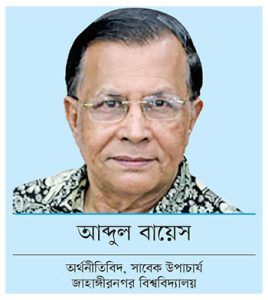বিশেষ প্রতিবেদন
মোহাম্মদ জাফর ইকবাল
১৬ মে ২০২৫
আইএমএফ বলেছে, ডলারের দাম বাজার নিয়ন্ত্রণ করলে এর প্রবাহ বেড়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়বে। অন্যদিকে রাজস্ব আয় বাড়লে সরকারের বিনিয়োগ বাড়বে। দেশের অর্থনীতিতে টেকসই প্রবৃদ্ধি হবে। তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত বাস্তবায়নের ফলে নিম্নমুখী মূল্যস্ফীতির হারে ফের চাপ বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। তাদের শর্ত অনুযায়ী ডলারের দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে ডলারের দাম বেড়ে যাবে, কমবে টাকার মান। মূল্যস্ফীতির হার সন্তোষজনক পর্যায়ে নেমে না আসা পর্যন্ত সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি অনুসরণ করতে হবে। এতে ঋণের সুদের হার বাড়বে, কমবে টাকার প্রবাহ। ফলে একদিকে বেসরকারি খাতে ঋণের জোগানও কমবে, অন্যদিকে ব্যবসা খরচ বাড়বে। এর প্রভাবে বাড়বে পণ্যের দাম। বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি কমাতে হলে দাম বাড়াতে হবে। ফলে সব পণ্য ও সেবার মূল্য বাড়বে। এসব কারণে মূল্যস্ফীতির হার আবার উসকে যেতে পারে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলেছে, ডলারের ওপর কড়া নজর রাখা হবে। যাতে কোনো ব্যাংক কারসাজি করে দাম বেশি বাড়াতে না পারে। কোনো ব্যাংক সংকটে পড়লে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ডলারের জোগান দেওয়া হবে। রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির কারণে ডলারের দাম বেশি বাড়বে না বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
গত বুধ ও বৃহস্পতিবার বাজারভিত্তিক বিনিময় হারে ডলার লেনদেন হয়েছে। এতে ডলারের দাম খুব বেশি বাড়েনি। তবে কিছু ব্যাংক ১২২ টাকা করে রেমিট্যান্স কিনে ১২৩ টাকায় বিক্রি করেছে। বেশির ভাগ ব্যাংকেই ডলারের দাম ১২২ টাকার মধ্যেই আছে। তবে আগাম বেচাকেনার ক্ষেত্রে দাম বেড়েছে।
বৈশ্বিক মন্দার কারণে ২০২২ সালের মার্চ থেকে দেশে মূল্যস্ফীতির হার বাড়তে থাকে। ওই বছরের আগস্টে তা বেড়ে ৯ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। গত বছরের জুলাই পর্যন্ত তা বেড়ে সর্বোচ্চ ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশে ওঠে। ওই মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৪ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বর্তমান সরকার দায়িত্ব নিয়ে নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়ায় এ হার এখন কমছে। গত এপ্রিলে ৯ দশমিক ১৭ শতাংশে নেমে এসেছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি নেমেছে ৮ শতাংশের ঘরে।
সূত্র মতে, মূল্যস্ফীতির হার কমাতে সরকার কঠোর মুদ্রানীতি অনুসরণ, ডলার বাজার স্থিতিশীল রাখা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে টাকা ছেড়ে সরকারকে ঋণের জোগান বন্ধ করা, পণ্যমূল্য কমানোর পদক্ষেপ নেয়। ফলে মূল্যস্ফীতির হার কমতে শুরু করেছে। তবে কঠোর মুদ্রানীতির কারণে সুদের হার বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ কম হওয়ায় বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থানের গতি কমে গেছে। এতে বেকারদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে।
আইএমএফের শর্ত অনুযায়ী ডলারের দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়ার কারণে বাড়বে ডলারের দাম, কমবে টাকার মান। এতে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমবে। বাড়বে পণ্যমূল্য। যা মূল্যস্ফীতিতে চাপ সৃষ্টি করবে। মূল্যস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত কঠোর মুদ্রানীতি অনুসরণ করতে হবে। এতে সুদের হার বাড়বে, টাকার প্রবাহ কমবে। ফলে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে। এমনিতেই এখন বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ তলনিতে রয়েছে। বিদ্যমান অস্থিরতা, সুদের হার বেশি ও ব্যাংকে তারল্য সংকটে বেসরকারি খাত ঋণ পাচ্ছে না। ফলে কর্মসংস্থান সংকুচিত হচ্ছে। এতে ভোক্তার আয় বাড়বে না। কিন্তু ব্যবসা খরচ বাড়ার কারণে পণ্যমূল্য বাড়বে। এতে মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ সৃষ্টি হবে।
আইএমএফ সরকারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণের শর্ত দিয়েছে। ফলে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে খরচ কমবে। এতে কষ্ট বাড়বে স্বল্প আয়ের মানুষের। যা তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দেবে। বিদ্যুৎ খাতে ব্যয় কমানো আইএমএফের অন্যতম একটি শর্ত। এটি বাস্তবায়ন করতে হলে বিদ্যুতের দাম বাড়াতে হবে। এর দাম বাড়লে সব খাতের পণ্য ও সেবার দামও বাড়বে। যা মূল্যস্ফীতিকে উসকে দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া আইএমএফ অনেকগুলো পরামর্শ দিয়েছে। যেগুলো বাস্তবায়ন হলে অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এর মধ্যে ব্যাংক খাতকে সবল করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি।
অর্থনীতিবিদরা বলছেন, প্রায় তিন বছর পার হতে চলল, অথচ মূল্যস্ফীতি নিয়ে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা কমছে না। বস্তুত সব সরকারেরই প্রথম টার্গেট থাকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার। কারণ এর ধকল সবচেয়ে বেশি বহন করে, গরিব শ্রেণি যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। দেশে গরিব খানাগুলো মোট আয়ের ৫০-৬০ ভাগ ঢালে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে চাল কেড়ে নেয় ৪০ ভাগ। তাই লাগামহীন মূল্যস্ফীতি বশে আনতে না পারলে সমাজের সমূহ খতির সম্ভাবনা থাকে, এমনকি ঊর্ধ্বগামী মূল্যস্ফীতি রাজনৈতিক ডিনামাইটে রূপ নিতে পারে। বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি কয়েক কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার নিচে ঠেলে দিয়েছে বলে বিভিন্ন গবেষণা বলছে। নিম্নআয়ের মানুষের প্রকৃত আয় পড়ে যাওয়াতে কম পুষ্টিকর খাবার কিনছে। সেই মানুষ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা বাদ দিচ্ছে। মোট কথা, মূল্যস্ফীতি মানব পুঁজি সৃষ্টিতে বাধা দিচ্ছে দীর্ঘমেয়াদে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাবেক ভিসি ও অর্থনীতি বিশ্লেষক আব্দুল বায়েস তার এক প্রতিবেদনে বলেছেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সমস্যার প্রকৃতি ও উৎস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া। বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতিকে উসকে দেয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে। বিশেষ করে খাদ্য, জ্বালানি, সার এবং মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার তির্যক অবমূল্যায়ন, যা ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর অবধি ৩০ শতাংশের মতো। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম কিছুটা হ্রাস পেলেও এই দুই উৎসের দ্বিতীয় পর্বের প্রভাব অনুভূত হতে থাকল। ২০২২ সালের আগস্ট মাসে সরকার র্কর্তৃক জ্বালানির দাম ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করেও লাভ হলো না। মূল্যস্ফীতির হার ১০ শতাংশের নিচে থাকলেও খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১২ শতাংশের ওপর চড়তে লাগল।
তিনি বলেন, যখন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে বাংলাদেশ ঠিক তখন হঠাৎ করেই মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। সম্ভবত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) চাপেই সরকার ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইনে কিছু সংশোধন আনতে যাচ্ছে। তবে সব অর্থমন্ত্রীর মতোই বর্তমান অর্থ উপদেষ্টা বলতে চাইছেন, আইএমএফের চাপে নয়, নিজেদের রাজস্ব আহরণের তাগিদেই বেশ কিছু পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ভ্যাট বসবে। তিনি আরও বলেছেন, যেসব পণ্যের ওপর অতিরিক্ত করের প্রস্তাব সেগুলো চাল, তেল , নুনের মতো অপরিহার্য নয় বিধায় মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ পড়বে বলে মনে হয় না, এগুলো শুল্ক শূন্য করলে দাম বাড়ার আশঙ্কা কম থাকবে। মূলত ভ্যাট বাড়লে সব পণ্য ও সেবার দাম বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমবে। নতুন করে সংকটে পড়বে ব্যবসা-বাণিজ্য।
অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা বলছেন, প্রত্যক্ষ কর বাড়ানোর মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বাড়ানো গেলে সবচেয়ে ভালো হতো। অবশ্য ব্যবসায়ীরাও বলছেন, এই মুহূর্তে ভ্যাট হার বাড়ানো হবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজস্ব আয় বাড়ার পরিবর্তে উল্টো কমতে পারে। কারণ হিসেবে তারা বলছেন, এমনিতেই মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার কারণে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। সেখানে জীবনরক্ষাকারী নিত্যপণ্যের ওপর ভ্যাট হার বৃদ্ধি মানুষকে আরও চাপে ফেলবে।
বাংলাদেশ কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি নাজের হোসাইন বলেন, সরকারের অন্তর্বর্তী পর্যায়ের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বাজার ব্যবস্থাপনা ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। যদিও সাম্প্রতিক কিছু পদক্ষেপ তা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণে এনেছে, তবুও বাস্তবতা হলো— সংকট এখনো পুরোপুরি কাটেনি। তবে মজুত বাড়ানো, চাল-গম আমদানিতে তৎপরতা, মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারি তদারকি বৃদ্ধি এবং কৃষকদের নিয়ে ভাবার উদ্যোগগুলো সাধারণ মানুষের মাঝে আশার আলো জাগাচ্ছে। বাজারব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান এবং ভোক্তা-সহনশীল মূল্যে নিত্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে এসব উদ্যোগ আরও প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন তিনি। একইসাথে আইএমএফ এর ভালো পরামর্শগুলোর বাস্তবায়নের উপরও দিনি জোরারোপ করেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, আমাদের আয় তো বাড়ছে না। কিন্তু ব্যয় তো বেড়েই চলেছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে আমাদের প্রকৃত আয় কমে যাচ্ছে। এখন আমাদের ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। ফলে আমাদের ঋণ নিলে কিন্তু শোধ করতেই হয়। আমাদের দেশে তো বেকার ভাতা নেই। আমাদের স্বাস্থ্যখাতে একটা বড় খরচ চলে যায়। অথচ উন্নত দেশগুলোতে দ্রব্যমূল্য বাড়লেও স্বাভাবিক জীবনে এর খুব বেশি প্রভাব পড়ে না। কারণ স্বাস্থ্য খাতে তাদের খরচ করতে হয় না। এসব কারণে আমাদের দেশে অনেক বেশি সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। তরুণেরা বিপথগামী হচ্ছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। কারণ তারা হাত পাততে পারে না। ফলে তাদের সঞ্চয় ভেঙে বা ঋণ করে চলতে হচ্ছে। আর সেই ঋণ শোধ করতে গিয়েই হচ্ছে সংকট।
জা ই / এনজি